 পতিত শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ ১৫ বছর শাসনামলে ভারতপন্থি হয়ে থাকার তকমা জোটে বাংলাদেশের কপালে। কিন্তু ২০২৪-এ ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী সরকারের পতন ঘটে। এখন সুযোগ এসেছে সেই ভারতপন্থি খোলস থেকে বেরিয়ে স্বকীয় পরিচয় তৈরী করার। সম্ভাবনার এই সময়ে একটি প্রশ্ন জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা হলো- দুই অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে সামলে কিভাবে নিজের দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। একথা এখন অনেকটাই সত্যি যে, বাংলাদেশের ওপরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা হাসিনা সরকার উৎখাতে মার্কিন সরকারের গেলো বাইডেন ভুমিকা রেখেছে। এদিকে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সব ধরনের চেষ্টা চালায় মার্কিন প্রসাশন। কিন্তু ওই বছরের ২৮ অক্টোবর পুলিশের নজিরবিহীন তান্ডবে বিএনপির মহাসমাবেশ ভেস্তে যাওয়ার পর সবাই বুঝতে পারে, এ দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে মার্কিন প্রশাসনের সকল তৎপরতা কোন কাজে আসেনি। এর ফলে ২০২৪-এর ৭ জানুয়ারি আওয়ামী সরকারের মিত্র প্রতিবেশী দেশের সরাসরি হস্তক্ষেপ, সমর্থন ও সহযোগিতায় ভোটারবিহীন একপাক্ষিক প্রহসনের নির্বাচন করে শেখ হাসিনাকে চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতার টিকিয় রাখে ভারত।
পতিত শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ ১৫ বছর শাসনামলে ভারতপন্থি হয়ে থাকার তকমা জোটে বাংলাদেশের কপালে। কিন্তু ২০২৪-এ ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী সরকারের পতন ঘটে। এখন সুযোগ এসেছে সেই ভারতপন্থি খোলস থেকে বেরিয়ে স্বকীয় পরিচয় তৈরী করার। সম্ভাবনার এই সময়ে একটি প্রশ্ন জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা হলো- দুই অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে সামলে কিভাবে নিজের দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। একথা এখন অনেকটাই সত্যি যে, বাংলাদেশের ওপরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা হাসিনা সরকার উৎখাতে মার্কিন সরকারের গেলো বাইডেন ভুমিকা রেখেছে। এদিকে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সব ধরনের চেষ্টা চালায় মার্কিন প্রসাশন। কিন্তু ওই বছরের ২৮ অক্টোবর পুলিশের নজিরবিহীন তান্ডবে বিএনপির মহাসমাবেশ ভেস্তে যাওয়ার পর সবাই বুঝতে পারে, এ দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে মার্কিন প্রশাসনের সকল তৎপরতা কোন কাজে আসেনি। এর ফলে ২০২৪-এর ৭ জানুয়ারি আওয়ামী সরকারের মিত্র প্রতিবেশী দেশের সরাসরি হস্তক্ষেপ, সমর্থন ও সহযোগিতায় ভোটারবিহীন একপাক্ষিক প্রহসনের নির্বাচন করে শেখ হাসিনাকে চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতার টিকিয় রাখে ভারত। 
আপাতত ভারতের হস্তক্ষেপে সেই সময়ের বাইডেন প্রশাসন হেরে গেলেও কূটনৈতিক শিষ্টাচার রক্ষায় মার্কিন প্রশাসন নির্বাচন পরবর্তী সময়ে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গেলো ১৫ বছরের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০৯ সালের পর থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পুরো সময় জুড়ে হাসিনা সরকারের প্রতি সমর্থন ছিলো মার্কিন প্রশাসনের। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় ২০২৩ সালের পরে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র একক কায়দায় স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের ক্ষমতা থাকার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। পরে দোটানায় আবারো হাসিনা সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য হয় দেশটি। এরপরে ৫ আগস্টের অভ্যত্থানে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ে যুক্তরাষ্ট্র। এ যাত্রায় সফল হয় তারা। অবিস্মরণীয় গণঅভ্যুত্থান ও বিপ্লবে হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হলে যুক্তরাষ্ট্র আর দেরী না করে ইউনূস সরকারের প্রতি সবধরণের সহযোগিতা দিতে এগিয়ে আসে।
বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন-ভারত সম্পর্কের ওপরও প্রভাব পড়ে। দু’দেশের দীর্ঘ সম্পর্কে টানাপেড়েন তৈরী হয়। কিন্তু ভারত হাল ছাড়েনি। দেশটি চেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে ভারত মার্কিন সম্পর্ক জোরদার করার। গেলো বাইডেন প্রশাসনের ডোনাল্ড ল্যু ও জ্যাক সুলিভানের ভারত সফরকে ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরী হয়েছিল। এ সময় এমন এক পরিবেশ তৈরী করা হয়- যাতে বাংলাদেশ প্রশ্নে মোদি-জয়শঙ্করের কথা শুনে সবাই মনে করতে পারে- এ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু একটা করতে চলেছে।
পরে মার্কিন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতায় এলে এ নিয়েও উচ্চ পর্যায়ের কর্তাদের ঘিরে ভারত একই রকমের আবহ তৈরির চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। একটু খেয়াল করলেই খুব সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব। ভবিষ্যতেও ভারত-মার্কিন কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে এই ধরণের কূটনৈতিক বৈঠক হলেই ভারত একই আবহ বারবার তৈরীর চেষ্টা করে যাবে। এদিকে, আবার চায়নাদের বিদেশ নীতি মার্কিন নীতির ঠিক বিপরীতে। তাদের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম একটি দিক হলো- তারা যে কোন সরকারের সঙ্গে সমান সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। সরকার নির্বাচিত বা অনির্বাচিত, তারা গণতান্ত্রিক নাকি স্বৈরতান্ত্রিক তা খুব একটা চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে ম্যাটার করে না। এছাড়া কোন দেশের স্বৈরাচারী শাসকের ভাল লাগা বা মন্দ লাগার প্রতিও চীন সংবেদনশীল। তারা নাখোশ হতে পারে এমন বক্তব্য, বিবৃতি দেয়া থেকেও বিরত থাকে তারা। এছাড়া স্বৈরাচারী কোন শাসকের বন্ধু ও প্রতিপক্ষের বিষয়েও যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করে সম্পর্ক বজায় রাখে চীন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে চীনের এই বিদেশ নীতির অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। তারা এখন মিয়ানমারে জান্তা ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সমঝোতার পথ খুঁজছে। একই রকমভাবে ২০২৩ সালে ইরান-সৌদি আরব সম্পর্কের মাঝে চীন মধ্যস্থতা করেছে চীন। তারও আগে ২০১৭ সালে জিবুতিতে নৌঘাটি স্থাপন করেছে চীন। দেশের বাইরে এটিই ছিল তার প্রথম সামরিক ঘাঁটি।
সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোটদানের ক্ষেত্রে চীনা নীতির পরিবর্তন দেখা যায়। এক্ষেত্রে চীন তার দীর্ঘদিনের নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যগ করে ভেটো প্রদান অব্যাহত রেখেছে। দেশটির এরকম নানা কাজের মাধ্যমে তাদের নীতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চীনকে মোকাবিলার তৎপরতা দেখা যায় সাম্প্রতিককালে। এ জন্যেই ভারতের সঙ্গে চীন বিরোধী কোয়াড ও ইন্দো-প্যাসিফিক জোট গঠন করেছে তারা। এদের তৎপরতা এখনও দৃশ্যমান না হলেও চীন বিরোধী অবস্থান শক্তিশালী করতেই তা গঠিত হয়েছে। চীন বিরোধী ভারত মার্কিনীদের অবস্থান সুষ্পষ্ট হলেও গেলো কয়েক দশক বাংলাদেশের সঙ্গে অব্যাহত রেখেছে দেশটি। বাংলাদেশে চীনের বিনিযোগ ও ঋণ দুই বেড়েছে। বাংলাদেশের প্রয়োজনেই চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রুখতে পারেনি পরাশক্তি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। এর কারণ, বাংলাদেশের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে ভারত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে চীনের আর্থিক সক্ষমতাবেশি। আর্থিক সক্ষমতার প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে চীনের তুলনাই চলে না। বরং ভারত নিজেই এখন আরও অধিক হারে চীনা ঋণ পেতে মুখিয়ে আছে। যদিও নরেন্দ্র মোদির সরকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে তা আড়াল করে রাখে।
এককালে চীন-ভারত শক্তিমত্তার তুলনা সূচক তর্কে উভয়ের সমকক্ষ হওয়ার ধারণা চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতকে যদি হাতি ধরা হয়, তবে চীনকে বলা চলে তিমি। এমনকি চীন তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও অগ্রগামী।
উদ্বৃত্ত অর্থ কিংবা সঞ্চয়ের পরিমাণ, অবকাঠামোগত প্রকল্পে ঋণ দান, নগদ অর্থ সহায়তা, ঋণ কিংবা সুদ মওকুফ, সুদ হার কমানো, সুদ ফেরত দানের কিস্তির সময়সীমাপুনঃনির্ধারণ ও বিলম্বিতকরণ এসব আর্থিক সক্ষমতায় চীন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে। বাংলাদেশের প্রয়োজন পূরণে চীনের এই সামর্থ্যকে শেখ হাসিনা সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আর ভারত-যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই এ বিষয়টি না দেখার ভান করে তাতে নীরবে সায় দিয়েছে। ৫ আগস্ট হাসিনার পতন হওয়া মাত্রই চীন নবগঠিত ইউনূস সরকারের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষমতা গ্রহণের পর গত ১২ অক্টোবর দুটি চীনা যুদ্ধজাহাজ শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশ ঘুরে যায়। হাসিনার পতনের পর চীনা কর্তৃপক্ষ হাসিনা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করতে থাকে। গত ৭ নভেম্বর চীনের আমন্ত্রণে বিএনপির ৪ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধি দল বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত পলিটিক্যাল পার্টি প্লাস কো-অপারেশন সম্মেলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় আলামত হলো, অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন গত ২০ জানুয়ারি চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা।
তার এই সফরকে প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদইউনূসের চীন সফরের প্রাক প্রস্তুতি বলা চলে। এখন প্রশ্ন হলো, চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের এই ঘনিষ্ঠতাকে যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে দেখবে? অর্থাৎ চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কত দূর পর্যন্ত গড়াতে পারবে? ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ধারণা করা হচ্ছিল, দুনিয়াজুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ও নেতৃত্ব আরও বহুকাল বিনা বাঁধায় চলতে থাকবে। সে সময় বলা হতে থাকে, নয়া আমেরিকান শতাব্দী শুরু হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের কবলে পড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহসাই উপলব্ধি করে চীন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে।
২০২২ সালের ৪ জানুয়ারি ভয়েস অব আমেরিকা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের শিরোনাম দেওয়া হয়- ২০৩০ সালের মধ্যেই চাইনিজ অর্থনীতি মার্কিন অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২১ সালে চীনের অর্থনীতি ১৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আর ওই বছর মার্কিন অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ২৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে ২০৩০ সাল পর্যন্ত চীনের বার্ষিক জিডিপিরপ্রবৃদ্ধি শতকরা ৪.৭% হারে চলতে থাকলে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রকে স্থানচ্যুত করে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র চীনা অর্থনীতির এই উত্থান ঠেকাতে ভীষণ তৎপর হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করতে চলেছেন, তা চীন-মার্কিন দ্বন্দ্বের চূড়ান্তবহির্প্রকাশ। এই দ্বৈরথে চীনের উত্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে অথবা চীন পরাজিত হয়ে মার্কিন শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন থাকতে পারে।
তবে পালাবদল যুগের এ সংঘাত বিশ্ব ব্যবস্থাকে প্রচন্ড নাড়া দেবে। আর যেহেতু এই পালাবদলের সংঘাতের ভরকেন্দ্র এশিয়া, তাই এ অঞ্চলের দেশগুলোর রাজনীতি ও অর্থনীতির আগের অবস্থানগত সমীকরণ এলোমেলো হতে থাকবে সবার আগে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের কৌশল হওয়া উচিত বলয়কেন্দ্রিক রাজনীতি পরিহার করা। চীনপন্থি কিংবা মার্কিনপন্থি হয়ে পড়া বাংলাদেশের জন্য আদৌ মঙ্গলজনক নয়।
বাংলাদেশের জন্য উত্তম পন্থা হলো, স্বদেশ ভাবনায় বিভোর থেকে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া। বিশেষ করে ভারতকে না জড়িয়ে বাংলাদেশ একাই পশ্চিমের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের অবকাঠামগত প্রকল্পে চীনা বিনিয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমকে বিচলিত করে তোলার কারণ নেই। কেননা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হলে এদেশে পশ্চিমা দেশগুলোর বিনিয়োগের পথকে সুগম ও নিষ্কণ্টক করে তুলবে না। ভঙ্গুর অবকাঠামো বিনিয়োগ পরিবেশের সবচেয়ে বড় বাধা। অতএব, বাংলাদেশ চীনা ঋণ গ্রহণ করে এবং একই সঙ্গে মার্কিন ও পাশ্চাত্য দেশের এফডিআইকে (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) সুযোগ দান করে উভয়কূল রক্ষা করতে পারে।
বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাঠামোগত সমঝোতা চুক্তি (টিকফা) এগিয়ে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে। বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলে, এদেশে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিমা পণ্যের ক্রেতা তৈরি হতে পারবে না। তাই চীনের তরফ থেকে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত ঋণ কিংবা নগদ অর্থ সহায়তা গ্রহণ যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখবে না। এভাবে চীন-মার্কিন দ্বৈরথে ভারসাম্যমূলক নীতি বজায় রাখার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। এককালে মার্কিন কিংবা সোভিয়েত বলয়ের বাইরের অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশসমূহকে তৃতীয় বিশ্ব বলে ডাকা হতো। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের স্থলে চীনের মুখে গ্লোবাল সাউথ নামটি প্রায়ই উচ্চারিত হচ্ছে। চীনের নেতৃত্বে গঠিত ব্রিকস জোট আইএমএফের আদলে আলাদা একটি ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়তে চায়। এছাড়া ব্রিকস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের একমাত্র বিনিময় মুদ্রা মার্কিন ডলারকে সরিয়ে দিয়ে নতুন মুদ্রা চালু করতে চায়।
ব্রিকসের মর্ম কথায় বলা হচ্ছে, সংস্থাটি গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর সঙ্গে উইন-উইন বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করবে। এভাবে চীন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু চীন কিভাবে এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দেবে তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। বিশ্ব নেতা হওয়া শুধু আর্থিক সক্ষমতা ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের ওপর নির্ভর করে না। বিশ্ব নেতা হতে চাইলে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষা, আন্তর্জাতিক বিচার কাঠামো প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা ও নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।
বিশ্ববাসীর সামনে চীন এখনও এ বিষয়গুলো তুলে ধরেনি। সন্দেহ নেই, বর্তমান দুনিয়ায় ভূরাজনীতির চেয়ে ভূঅর্থনীতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চীনের আর্থিক সক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব অপর দেশের ওপর ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু ১৯৪৫ সালের পর থেকে বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদার গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার যেসব কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তৈরি করেছে, তার বিকল্প ধারণা ও ব্যবস্থা চীন উপস্থাপন করতে পারেনি। এটাই চীনের বিশ্বনেতা হওয়ার প্রধান অন্তরায়।
যুক্তরাষ্ট্র আরও দীর্ঘকাল বিশ্বনেতা হিসাবে টিকে থাকবে কিনা অথবা চীন তাকে টপকে যাবে কিনা সেই ফয়সালা চটজলদি দৃশ্যমান হবে না। এ লড়াই দীর্ঘ কয়েক দশক পর্যন্ত চলতে পারে। বস্তুত পরিবর্তনের গতিরোধ করার কর্তৃত্ব কারও একক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা প্রাকৃতিক ঘটনার মতোই কারও কর্তৃত্ব ছাড়াই সংঘটিত হয়ে যায়। চীন বিনা বাধায় একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে না।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনা উত্থান ঠেকানোর তৎপরতার অভিঘাত অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও রাজনৈতিক উত্তেজনা-অস্থিরতা তৈরি করবে। সেই চাপ মোকাবিলায় কিভাবে ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণের কৌশল অবলম্বন করা যায়। সেজন্য জাতীয় নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রস্বার্থ রক্ষা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। বাংলাদেশ রয়েছে ভারতীয় আধিপত্যবাদের ঝুঁকিতে। ভারতীয় আধিপত্যবাদের আতঙ্ক থেকেই এদেশের জনমত চীনের সঙ্গে সখ্যগড়তে আগ্রহী।
রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে চীন মিয়ানমারকে বাধ্য করতে পারলে চীন-বাংলাদেশ আরও গভীর সম্পর্ক তৈরি হতে পারবে। অন্যদিকে চীন-মার্কিন দ্বৈরথে বাংলাদেশ শামিল না হয়ে বরং চীন-যুক্তরাষ্ট্র বৈরিতা নিরসনে বাংলাদেশ সেতুবন্ধের ভূমিকা পালন করতে পারে। এদেশ হতে পারে পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ মীমাংসার নিরপেক্ষ কেন্দ্রভূমি। ঢাকা হতে পারে শান্তি সংলাপের কেন্দ্রস্থল। তবে এর জন্য এদেশে প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্ব ও যথাযথ কর্মকৌশল।
এই পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস চার দিনের সরকারি সফরে গত বুধবার চীনে যান। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি অধ্যাপক ইউনূসের প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফর। এই সফরে দু’দেশ তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরো গভীর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তিতে উভয় দেশ বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় বৃদ্ধিতেও একমত হয়েছে। চীনের উপ প্রধানমন্ত্রী ডিং শুয়ে শিয়াং হাইনানের উপকূলীয় শহরে বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়া বার্ষিক সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং পরে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উপ প্রধানমন্ত্রী ডিং বলেন, প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং আপনার সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছেন। তিনি আরো বলেন, চীন আশা করে, প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সমৃদ্ধি অর্জন করবে।
বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওয়ান চায়না নীতি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন, চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে যোগ দেওয়া প্রথম দক্ষিণ এশীয় দেশ হিসেবে ঢাকা গর্ব অনুভব করে। বৈঠকে বাংলাদেশ বিভিন্ন উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রকল্পে চীনের সহায়তা চেয়েছে এবং চীনা ঋণের সুদের হার ৩ শতাংশ থেকে ১-২ শতাংশে নামিয়ে আনার অনুরোধ করেছে।
এ ছাড়া বাংলাদেশ চীনা অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর কমিটমেন্টফিমওকুফের আহ্বান জানিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা চীনের তৈরি পোশাক কারখানা, বৈদ্যুতিক যানবাহন, হালকা যন্ত্রপাতি, উচ্চ প্রযুক্তির ইলেকট্রনিকস, চিপউৎপাদন এবং সৌর প্যানেল শিল্প বাংলাদেশে স্থানান্তর সহজ করতে বেইজিংয়ের সহায়তা চান। উপ প্রধানমন্ত্রী ডিং শুয়ে শিয়াং জানান, ২০২৮ সাল পর্যন্ত চীনে বাংলাদেশি পণ্য শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে, যা বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের দুই বছর পর পর্যন্ত বহাল থাকবে।
এ বছরের গ্রীষ্মকাল থেকেই বাংলাদেশ থেকে চীনে আম রপ্তানি শুরু হবে। বেইজিং কাঁঠাল, পেয়ারা এবং অন্যান্য জলজ পণ্য আমদানি করতেও আগ্রহী, যাতে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্যের বিশাল ব্যবধান কমানো যায়। চীনা সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আরো বেশি স্কলারশিপ প্রদান করবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই হাজার হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে।
উপ প্রধানমন্ত্রী ঢাকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের জন্য চারটি সমুদ্রগামী জাহাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে চীনের অর্থায়নের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের প্রচেষ্টায় চীন বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে নিয়ে সংলাপ করবে। প্রফেসর ইউনূস চীনের নেতৃত্বের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই বৈঠক ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশ-চীন অংশীদারির আরেকটি মাইলফলক চিহ্নিত করল। তিনি বলেন, আসুন, আমরা একসঙ্গে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করি যাতে আমাদের দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয় এবং বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক অংশীদারির একটি নতুন যুগের সূচনা হয়।
এরপর সফরের অংশ হিসেবে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের মধ্যে একটি অত্যন্ত সফল দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়। বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে তাঁরা দ্বিপক্ষীয়স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মধ্যে একটি অত্যন্ত সফল দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা হয়েছে। ফলপ্রসূ ও গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। সি চিন পিং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি চীনের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সি চিন পিং বলেছেন, বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ উৎসাহিত করবে চীন। চীনা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশে স্থানান্তরকে উৎসাহিত করবে। বাংলাদেশের উত্থাপিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চীন ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করবে। এর মধ্যে চীনা ঋণের সুদের হার হ্রাস ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার বিষয় রয়েছে। সব মিলিয়ে ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয়ের বাইরে এসে বাংলাদেশ স্বকীয় অর্থনৈতিক বলয় গড়ে তুলবে এমন প্রত্যাশা আপামর জন সাধারণের।
লেখক: কবি, সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব
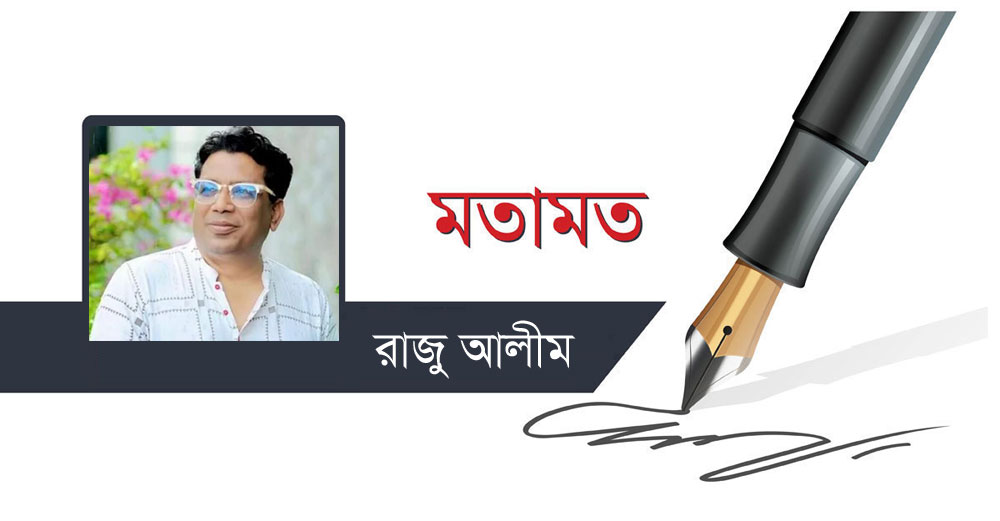
 পতিত শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ ১৫ বছর শাসনামলে ভারতপন্থি হয়ে থাকার তকমা জোটে বাংলাদেশের কপালে। কিন্তু ২০২৪-এ ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী সরকারের পতন ঘটে। এখন সুযোগ এসেছে সেই ভারতপন্থি খোলস থেকে বেরিয়ে স্বকীয় পরিচয় তৈরী করার। সম্ভাবনার এই সময়ে একটি প্রশ্ন জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা হলো- দুই অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে সামলে কিভাবে নিজের দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। একথা এখন অনেকটাই সত্যি যে, বাংলাদেশের ওপরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা হাসিনা সরকার উৎখাতে মার্কিন সরকারের গেলো বাইডেন ভুমিকা রেখেছে। এদিকে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সব ধরনের চেষ্টা চালায় মার্কিন প্রসাশন। কিন্তু ওই বছরের ২৮ অক্টোবর পুলিশের নজিরবিহীন তান্ডবে বিএনপির মহাসমাবেশ ভেস্তে যাওয়ার পর সবাই বুঝতে পারে, এ দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে মার্কিন প্রশাসনের সকল তৎপরতা কোন কাজে আসেনি। এর ফলে ২০২৪-এর ৭ জানুয়ারি আওয়ামী সরকারের মিত্র প্রতিবেশী দেশের সরাসরি হস্তক্ষেপ, সমর্থন ও সহযোগিতায় ভোটারবিহীন একপাক্ষিক প্রহসনের নির্বাচন করে শেখ হাসিনাকে চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতার টিকিয় রাখে ভারত।
পতিত শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ ১৫ বছর শাসনামলে ভারতপন্থি হয়ে থাকার তকমা জোটে বাংলাদেশের কপালে। কিন্তু ২০২৪-এ ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী সরকারের পতন ঘটে। এখন সুযোগ এসেছে সেই ভারতপন্থি খোলস থেকে বেরিয়ে স্বকীয় পরিচয় তৈরী করার। সম্ভাবনার এই সময়ে একটি প্রশ্ন জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা হলো- দুই অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে সামলে কিভাবে নিজের দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। একথা এখন অনেকটাই সত্যি যে, বাংলাদেশের ওপরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা হাসিনা সরকার উৎখাতে মার্কিন সরকারের গেলো বাইডেন ভুমিকা রেখেছে। এদিকে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সব ধরনের চেষ্টা চালায় মার্কিন প্রসাশন। কিন্তু ওই বছরের ২৮ অক্টোবর পুলিশের নজিরবিহীন তান্ডবে বিএনপির মহাসমাবেশ ভেস্তে যাওয়ার পর সবাই বুঝতে পারে, এ দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে মার্কিন প্রশাসনের সকল তৎপরতা কোন কাজে আসেনি। এর ফলে ২০২৪-এর ৭ জানুয়ারি আওয়ামী সরকারের মিত্র প্রতিবেশী দেশের সরাসরি হস্তক্ষেপ, সমর্থন ও সহযোগিতায় ভোটারবিহীন একপাক্ষিক প্রহসনের নির্বাচন করে শেখ হাসিনাকে চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতার টিকিয় রাখে ভারত। 